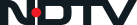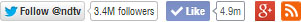- Home/
- দুর্গাপুজোর ইতিহাস- তোষামদ থেকে স্তাবকতা ভায়া জাতীয়তাবাদ বিবর্তনের দুর্গাপুজো
দুর্গাপুজোর ইতিহাস- তোষামদ থেকে স্তাবকতা ভায়া জাতীয়তাবাদ বিবর্তনের দুর্গাপুজো

ক্যালেন্ডার পেয়েই প্রথম দুর্গাপুজোর ছুটি দেখতে বসাটা বোধহয় এখনও গেল না গেল না করে রয়েই গেছে বাঙালির। যে যার মতো করে অন্তত ওই চারদিনের জন্য অল্পবিস্তর পরিকল্পনা করেই থাকেন। দুর্গাপুজো নিয়ে বাঙালির সেন্টিমেন্টে প্রাথমিক ভাবে হয়ত তেমন বদল আসেনি, উদযাপনে ফারাক এসেছে প্রজন্মের নিয়মেই। তবে পুজোর রাজনৈতিক চরিত্রে বিবর্তনের বাঁকগুলো বদলে যাচ্ছে দ্রুত। তোষামুদে পুজো থেকে শুরু করে আজকের কার্নিভালপুজো- পালটে যাওয়ার গল্পের মাঝের ব্যবধান প্রায় দু' তিনশো বছর।
বৈদিক এবং আদিবাসী দেবদেবীদের মধ্যে ‘মা' ধারণার পুজো ছিল প্রথম থেকেই। কিন্তু যেভাবে এখন, যে আচারে-আয়োজনে দুর্গাপুজো দেখতে আমরা অভ্যস্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত হিন্দুদের মূর্তিপুজোয় দুর্গাকে এই রূপে পুজো করার উল্লেখই তেমন নেই। দুর্গাকে এমন ঘরের মেয়ে করে পুজো করার উল্লেখ আমরা পাই সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে। এসবের মধ্যে আবার অদ্ভুত ভাবে জড়িয়ে রয়েছে পলাশীর যুদ্ধ। হ্যাঁ, বিশ্বাসঘাতকতার ঐতিহাসিক উদাহরণ বা বাংলায় ইংরেজ শাসনের ইতিহাসের সূত্রপাত হিসেবেই শুধু নয়, বাংলায় এইভাবে দুর্গাপুজোর শুরু এবং বিস্তারের নেপথ্যেও পলাশীর যুদ্ধের ভূমিকা অনেকটাই।
মুঘলদের থেকে পৃথক হয়ে নবাবরা বাংলা শাসন করার সময়থেকেই এই অঞ্চলে হিন্দু জমিদারদের উদ্ভব হয়। আস্তে আস্তে এই জমিদাররা নিজেদেরই ক্ষমতাবলে হয়ে ওঠেন প্রাদেশিক রাজা। নামে যখন রাজা তখন প্রজাদের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখাও রাজার অধিকারেই পড়ে। বলা বাহুল্য, এই প্রাদেশিক রাজারা নিজেদের ক্ষমতাবান মনে করলেও আসলে কিন্তু নবাবদের হাতেই ছিল ক্ষমতার মূল রাশ। এই গোটা ছবিটা পালটে যায় ১৭৫৭র পর থেকেই।
পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে নবাবদের হার শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতার ক্ষেত্রেই নয় সামাজিক জীবন যাপনেও অদ্ভুত বদল আনে। যুদ্ধের পরপরই প্রাদেশিক রাজাদের এক ছদ্ম ক্ষমতায়ন ঘটে। এতদিন প্রজাদের শাসন করলেও আসল ক্ষমতা ছিল বকলমে নবাবদের হাতেই। প্রাদেশিক রাজাও জানতেন জমিদারের ভূমিকায় আসলে এ কেবলই রাজা-রাজা খেলা।
ইংরেজদের জয় এবং রাজ্য শাসনের মূল জায়গায় তাঁদের প্রবেশ এই জমিদারদের মনে দীর্ঘদিনের লালিত অভীপ্সায় (লোভও বলা যায়) নতুন করে নাড়া দেয়। প্রজাদের খানিক নিজের বশে রাখা এবং মালিক ইংরেজদের তোষামোদে রাখতে দুর্গাপুজোকে সামনে নিয়ে আসেন জমিদাররা। প্রায় সমস্ত জমিদার বাড়িতেই ঘটা করে দুর্গাপুজোর আয়োজন হতে থাকে। বেশ কয়েকদিন ধরেই জমিদার বাড়িতে চলত জাঁকজমকের পুজো, খাওয়াদাওয়া এবং অনুষ্ঠান। পুজোকে উপলক্ষ করে জমিদারিত্বের মেয়াদ বাড়ানো এবং সুনজরে থেকে শাসকের অধীনে ছোট শাসক হয়ে ওঠাই ছিল প্রাদেশিক রাজাদের পাখির চোখ।

পুরনো কলকাতার পুজো
শোনা যায়, পলাশীর যুদ্ধে নবাবদের হারানোর পরে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাতে চেয়েছিলেন রবার্ট ক্লাইভ। কিন্তু কলকাতা শহরের একমাত্র চার্চটি নবাবরা ধ্বংসকরে ফেলায় সেই পথ বন্ধ হয়ে যায়। তখন ক্লাইভের ব্যক্তিগত সচিব নবকৃষ্ণ দেব তাঁর বাড়িতেদুর্গাপুজোয় ক্লাইভকে আমন্ত্রণ জানান। ধুমধাম করে পুজো হয় কলকাতায় শোভাবাজারে নবকৃষ্ণেরবাড়িতে। যদিও মনে করা হয়, এই ক্লাইভ এবং দুর্গাপুজোর এই গল্পটি নবকৃষ্ণের নিজের মতোকরে তৈরি করে নিয়েছিলেন। তবুও, পুরনো কলকাতার ইতিহাস ঘাটলেই দেখা যায় শোভাবাজার রাজবাড়িরপুজোকে ‘কোম্পানির পুজো' বলেই উল্লেখ করা হয়েছে বিভিন্ন জায়গায়।
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাজের সাথে তাল মিলিয়েই বাণিজ্যের সুবিধার জন্য কলকাতা এবং তার আশেপাশের এলাকায় শহর জন্মায়। মূলত ব্যবসাকে ঘিরে গড়ে ওঠা এই শহর এবং তার আশপাশ লাগোয়া বড় অংশেই ব্যবসায়ী গোষ্টীরও জন্ম হয় সেই সময়েই। সদ্য জন্মানো শহরে সদ্য জন্মানো বাঙালি ব্যবসায়ীদের চরিত্র নিয়ে খুব বেশি শব্দ খরচ না করলেও এটুকু বলা যায় সাদা চামড়ার আনুগত্য এবং লক্ষ্মীর বসতি পাকা করতে দুর্গাপুজো আবারও এক অস্ত্রই হয়ে ওঠে। ব্যাপারটা অনেকখানা বাড়ির সত্য নারায়ণ পুজোয় প্রবাসী ভারতীয় বসকে আমন্ত্রণ করে খাওয়ানোর মতো। তাতে পাড়াপড়শির কাছে যেমন ইজ্জত বাড়ে, বসের গুডবুকেও নাম পাকা হয়। এখনকার পুজোর কম্পিটিশন, উৎস খুঁজলে দেখা যায় এও সেই আমলেরই। দুই বড় ব্যবসায়ীর পুজোর টক্কর মোড়ক পাল্টেছে কেবল, চরিত্র নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ঠাকুর পরিবার এবং শিবকৃষ্ণ দাঁ-দের গন্ধবণিক পরিবারের দুর্গাপুজোর গল্প। এই দু'খানা পুজোই ছিল সেই সময়ের নিরিখে ‘বড় বাজেটের' পুজো। প্রতিমার সোনার গয়না, দামী রত্নের মুকুট থেকে শুরু করে ঘটা করে লোক খাওয়ানো কিছুই বাকি ছিল না। এমনকি সাহেবদের মনোরঞ্জনের জন্য পুজোর ক'দিন অনুষ্ঠানে নাচের মুর্শিদাবাদ, লক্ষ্ণৌ থেকে নাচিয়েদেরও নিয়ে আসা হত জমিদার বাড়িতে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিরই এক কর্মচারী J H Holwell- এর কথায়, বাঙালিদের এই পুজোয় ইউরোপীয়দের নিমন্ত্রণকরার পিছনে আরেকটা কারণ ছিল এই যে, অনেক ইংরেজই সেই সময় এই পুজোগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।প্রায় অর্ধেক মাস জুড়ে চলত উৎসব। মরশুমি ফল আর ফুলদিয়ে সাহেবদের অভ্যর্থনা জানান হত। সাহেবদের জন্যই পুজোর প্রতিদিন বসত গান নাচের আসর।
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুরসময়ে আবার চরিত্র পালটায় দুর্গাপুজো। এতকাল যা ছিল শ্বেতাঙ্গদের মনোরঞ্জনের কারণ হঠাৎইভূমিকা পালটে তা হয়ে ওঠে ইংরেজ হঠাওয়ের অন্যতম অনুঘটক। ভারতে, বিশেষ করে বাংলায় স্বাধীনতাআন্দোলনের শুরুর এই সময়ে বাড়ির মেয়ের খোলস বদলে দুর্গাকে যেন দেশমাতার ভূমিকাতেই বেশিকরে ভাবতে চান বিপ্লবীরা।অবশ্য শুধু দেশমাতা বললে ভুল হবে। ইংরেজদের শাসন থেকে দেশকেবাঁচাতে একদিকে দেবী দুর্গাই হয়ে ওঠেন শক্তির প্রতীক। আবার অন্যদিকে দুর্গাই হয়ে ওঠেদেশ। দেশ মানে মাতৃভূমি, মায়ের ভূমিকে রক্ষাই যেন হয় বিপ্লবীদের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান এবং লক্ষ্য। ইতিহাসবিদের মতে, দুর্গার এই চরিত্র বদলের পিছনে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস ‘আনন্দমঠে'র (১৮৮২ সালে লেখা) ভূমিকা অসামান্য।সন্ন্যাসী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা এই উপন্যাসেইদুর্গাকে বা বলা ভাল শক্তির বিভিন্ন মৃণ্ময়ী রূপকে আন্দোলনকারীরা কীভাবে দেশের সাথেএকই স্থানে রাখছেন তা একেবারেই স্পষ্ট। জগদ্ধাত্রীর সঙ্গে ইংরেজ শাসনের আগের দেশের রূপ, কালীর সঙ্গে বর্তমান দেশের হাল এবং আসলে আমাদের দেশের কী হওয়া উচিত তার রূপ দুর্গারপ্রতিমার মধ্য দিয়েই প্রকাশ করেন বঙ্কিম। উপন্যাসে ব্যবহৃত ‘বন্দেমাতরম' গান বিপ্লবীদেরলড়াইয়ের অন্যতম মন্ত্র। বাঙালি-চালিত প্রেসগুলিতে দুর্গা প্রতিমার ছবির উপর বহু দেশাত্মবোধকগান ছাপা হয়। সেই সময়েই লর্ড কার্জনের শিক্ষানীতির বিরোধিতা করে বিভিন্ন পত্রিকায় পুজোবিষয়ক লেখাতেও দুর্গার এই দেশমাতায় বিবর্তনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। ইংরেজদের শাসনেতাঁর সন্তানদের দূর্বিষহ যাপন, খরা, বন্যা এবং দুর্গতি থেকে মুক্তির জন্য দুর্গতিনাশিনীহিসেবে দুর্গার উল্লেখ রয়েছে ১৯০৩ সালে প্রকাশিত পত্রিকা বেঙ্গলিতেও।
১৯০৫সালে বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার পরেই সম্ভবত দুর্গাপুজোয় গুরুত্বপূর্ণ বদল আসে। স্বদেশী আন্দোলনের ব্যপ্তি বাড়াতে এই উৎসবই বিপ্লবীদের কাছে হয়ে ওঠে প্রয়োজনীয় হাতিয়ার। প্রায় প্রতিটা পুজোর বিজ্ঞাপনেই নজরে আসে ‘নাথিং বিদেশী, এভরিথিংস্বদেশী' জাতীয় পাঞ্চলাইন। সকলের জন্য এবং সকলকে নিয়ে সার্বজনীন দুর্গাপুজোর ধারণাটিও শুরু হয় এই সময় থেকেই।বলা হয়, উত্তর কলকাতার মানিকতলাতেই প্রথম সর্বজনীন দুর্গাপুজোর শুরু, সেই সময় যার ডাকনাম ছিল ‘কংগ্রেস পুজো'। এমনকী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেরসময় জেলের মধ্যে থেকেও বিপ্লবীদের দুর্গাপুজোর আয়োজনের দাবি জানিয়েছেন এমন উদাহরণও রয়েছে প্রচুর। ১৯২৫-এর সেপ্টেম্বর মাস। জেলে বসেই বন্ধুকে চিঠি লেখেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। জানান, জেলের মধ্যে থেকেও পুজোর আয়োজনের অনুমতি মিলেছে। সেই সময়ে পুজো কেন্দ্র করে লাঠিখেলার মতো প্রদর্শনী চালু হয়। যা আদতে বিপ্লবীদের অনুশীলনেরই অঙ্গ ছিল। সেই প্রথা মেনে আজও বাগবাজারে অষ্টমীর দিন বীরাষ্টমী পালন হয়। স্বদেশী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সিমলা ব্যায়াম সমিতির পুজোয় প্রতিমাকে তখন খাদি বস্ত্র পরানো হতো। পুতুল ও অন্যান্য খেলার প্রদর্শনীর মাধ্যমে রাজনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরা হতো।
তোষামোদের আয়োজন থেকে বিপ্লবের সাথে সাধারণ মানুষের অন্তর্ভূক্তির পন্থা হিসেবে দুর্গাপুজোয় বিবর্তনের আঁচড়গুলো নিঃসন্দেহে স্পষ্ট। তবে নেহাতই এই সময়ের প্রেক্ষিতে পুজো নিয়ে বিশ্লেষণ করতেগিয়ে যদি বলি, তোষামোদ এবং তাবেদারির উদ্দেশ্যই কেমন যেন মুখ্য হয়ে উঠছে আবার এই একবিংশশতাব্দীতে- খুব একটা ভুল হবে না।শাসক বদলালেউৎসবেরও চরিত্র বদল হয়। ক্লাইভকে তুষ্ট করা হোক বা জমিদারিত্ব পাকা করতে টেক্কা দেওয়া ঝাড়লণ্ঠন আর দামী কারণবারির আয়োজন কোথাও যেন ঘুরেফিরে মিশে যাচ্ছে এইসময়ের থিম-টক্করেরসঙ্গে। শাসকের মুখের উপর কখনও সুপারিম্পোজ হতে থাকে ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেলের আদল, কখনও বা বর্তমান রাজনৈতিক দলের ঝাণ্ডার রঙ। গল্প আসলে একই। বহুকালের শিকড়ওয়ালা একটা উৎসব, পোশাক বদলে বদলে হয়ে উঠছে কার্নিভ্যাল। একটা সাধারণ উদ্দেশ্যে বিপ্লবের সঙ্গে মানুষের অন্তর্ভূক্তির তাগিদ আর দুর্গাপুজোর নেপথ্য নয়, বরং পুজো নিজেই এখন বহু শিল্প এবং শিল্পীর বেঁচে থাকার নেপথ্যের গল্প।
বাংলার সেরা পুজো
আরও দেখুন- Thursday October 18, 2018 , কলকাতা
বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান ও পুজোয় শোলার ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু শিল্পীরা সাধারণত প্রচারের আলোর বিপরীতেই রয়ে যান।
- NDTV | Wednesday October 17, 2018 , কলকাতা
পুজোর মাধ্যমে দেবী দুর্গাকে বার্তা দেওয়া হচ্ছে মা যাতে এসে কালো অশুভ হাতের বিনাশ করেন। আর মায়ের সেই বিনাশ মূর্তির মধ্যে দিয়েই জেগে উঠুক নতুন প্রাণ।
- NDTV | Tuesday October 16, 2018 , কলকাতা
পুজো প্যান্ডেল তৈরি হল এক বিশেষ দাবিকে সামনে রেখে। না কোনও রাজনৈতিক বা সামাজিক দাবি নয়, এই দাবি একেবারেই শহুরে, কলকাতাকে ভালবাসার প্রতীক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শহর, কলকাতার পরিচিতি সিটি অফ জয় নামে। কিন্তু আয়োজকরা চান কলকাতা পরিচিত হোক সাহিত্যের শহর হিসেবে। তাই এবার রাজা রামমোহন সরণির চালতা বাগানের পুজোর থিম বিশ্বকবি। 76 বছরে পা দেওয়া চালতাবাগানের থিমের পোশাকি নাম কবিগুরুর শান্তিনিড়। উদ্দেশ একটাই ইউনেস্কোর থেকে স্বীকৃতি আদায় করে নেওয়া।
- Monday October 15, 2018 , কলকাতা
সাদার্ন নুকের দুর্গাপুজোর এ বার ১০ বছরে পা। তবে এই আবাসনের পুজোয় এ বার রয়েছে নতুন স্পেশ্যালিটি। এ বার মায়েদের হাতেই জগজ্জননীর পুজোর ভার ন্যস্ত।
বিদেশের পুজো
আরও দেখুন- Tuesday October 16, 2018 , কলকাতা
সূদূর জার্মানির বার্লিন শহরে বসেও দুর্গাপুজোর উৎসবে মাতোয়ারা একদল ভারতীয়। পুজোর আয়োজন থেকে উপকরণ কোথাও নেই এতটুকু কার্পণ্য।
- NDTV | Monday October 15, 2018 , নিউ দিল্লি
পিপলস ফ্রেন্ডশিপ ইউনিভার্সিটি অফ রাশিয়া ইন্টার ক্লাবে এবছর ধুমধাম করে আয়োজিত হচ্ছে মস্কোর দুর্গাপুজো। 15 অক্টোবর থেকেই শুরু হয়ে যাচ্ছে উদযাপন। 19 অক্টোবর পর্যন্ত চলবে নানা অনুষ্ঠান।
- Surajit Ghosh | Friday October 05, 2018 , কলকাতা
বর্ধমানের সুমিত কোঙার। আপাতত এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিষয়ে পোস্ট ডক করছেন। বছর দুয়েক হল বিলেতে আছেন। সেখানে গিয়েই বুঝেছেন নতুন জায়গায় গিয়ে পুজোর ব্যাপারে খোঁজ খবর পেতে বেশ বেগ পেতে হয়। বিলেতের এদিক ওদিকে থাকা ভারতীয় তথা বাঙালিরা জানতেই পারেন না, ঠিক কোথায় হচ্ছে পুজো। সেই সমস্যা থেকেই মুক্তি দিতেই উদ্যোগ নিলেন সুমিত।